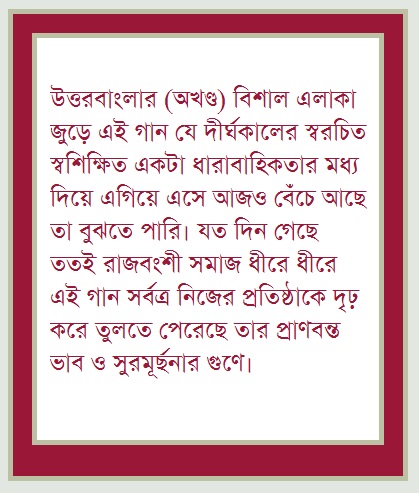 একদিন প্রকৃতির সঙ্গে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষকে আলাদা
করে শনাক্ত করা যথেষ্ট কঠিন ছিল। প্রকৃতির সন্তান হিসেবে উন্মুক্ত খোলা
হাওয়া সবুজ মাঠ-বনানী নদীর চর ছিল তার জীবন ও আত্মার প্রিয় লীলাভূমি। বুকের
ভেতর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উঠে আসতো অকপট অনাবিল সুর ও শব্দ। সেই সুর ও
শব্দ ছিল তাদের সরল সহজ ব্যক্তিচরিত্রের দ্যোতক স্বরূপ। স্বভাবতঃই রাজবংশী
নারী-পুরুষের হৃদয়ের ভাব ও আবেগ সেই সুর ও শব্দের সম্মিলনে হয়ে উঠতো
মর্মস্পর্শী। ভাবপ্রধান এই হৃদয়স্পর্শী সুর ও শব্দ মিলে মিশে যে
সুরমূর্ছনার জন্ম হয়েছিল তার লগ্নমুহূর্ত আমাদের ঠিকঠাক জানা না থাকলেও
নানান বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে অনুমান করা যায় তা ভাওয়াইয়া গান হিসেবে
সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকে পরিচিতি লাভ করেছিল। এ প্রসঙ্গে
একটা প্রাচীন ছড়ার উল্লেখ করা যেতে পারে যেটি হরিশচন্দ্র পাল মশাই তাঁর দুই
খণ্ডের বিখ্যাত ভাওয়াইয়া গানের সঙ্কলনে রেখে গেছেন,
একদিন প্রকৃতির সঙ্গে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষকে আলাদা
করে শনাক্ত করা যথেষ্ট কঠিন ছিল। প্রকৃতির সন্তান হিসেবে উন্মুক্ত খোলা
হাওয়া সবুজ মাঠ-বনানী নদীর চর ছিল তার জীবন ও আত্মার প্রিয় লীলাভূমি। বুকের
ভেতর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উঠে আসতো অকপট অনাবিল সুর ও শব্দ। সেই সুর ও
শব্দ ছিল তাদের সরল সহজ ব্যক্তিচরিত্রের দ্যোতক স্বরূপ। স্বভাবতঃই রাজবংশী
নারী-পুরুষের হৃদয়ের ভাব ও আবেগ সেই সুর ও শব্দের সম্মিলনে হয়ে উঠতো
মর্মস্পর্শী। ভাবপ্রধান এই হৃদয়স্পর্শী সুর ও শব্দ মিলে মিশে যে
সুরমূর্ছনার জন্ম হয়েছিল তার লগ্নমুহূর্ত আমাদের ঠিকঠাক জানা না থাকলেও
নানান বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে অনুমান করা যায় তা ভাওয়াইয়া গান হিসেবে
সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকে পরিচিতি লাভ করেছিল। এ প্রসঙ্গে
একটা প্রাচীন ছড়ার উল্লেখ করা যেতে পারে যেটি হরিশচন্দ্র পাল মশাই তাঁর দুই
খণ্ডের বিখ্যাত ভাওয়াইয়া গানের সঙ্কলনে রেখে গেছেন,
‘সারিঞ্জা বাজায় সাউদ সওদাগর
বাঁশী বাজায় চোর
বেনা বাজায় ত্যানা পিন্দা
দোতরা হারামখোর।’
এই ছড়ায় ব্যবহৃত শব্দ এবং উদ্দেশ্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই ছড়াকারের সঙ্গে
গান-বাজনা এবং উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের সমাজ ও জীবন
সম্পর্কে কোনরকম ধারণা শ্রদ্ধা কিংবা সম্মানবোধ ছিল না। ‘হারামখোর’ শব্দটিও
এতদ্দেশীয় শব্দ নয়।
গান-বাজনা যাদের ধর্মীয় জীবনে নিষিদ্ধ বলে মনে করা হয় এবং যে গান নর-নারীর
প্রেম-পীরিত সম্পর্কেই উচ্চারিত বলে পরিত্যাজ্য বলে যারা মনে করে, এই ছড়া
তাদেরই প্রচারিত বলে মনে হওয়া সম্ভব। স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে উত্তরবঙ্গের
মাটিতে দাঁড়িয়ে উত্তরবঙ্গের প্রাণের গান সম্পর্কে এই স্পর্ধিত প্রচারের
পেছনে রাজশক্তির প্রচ্ছন্ন মদত থাকাও অসম্ভব নয়। উচ্চবর্ণ শাসিত সামাজিক
ব্যবস্থায় (প্রাচীন কামতাপুর কিংবা কোচবিহার-রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতা তো দূর,
উপেক্ষা আর অবহেলাই ছিল ভাওয়াইয়া গানের অদৃষ্ট) ব্রাত্যজনের ভাব প্রকাশের
মাধুর্য যতই হৃদয়স্পর্শী হোক না কেন কয়েক’শো বছরেও তা জাতে ওঠে নি। তাই
রাখাল কিশোর কিংবা ‘হালুয়া’র গান সম্পর্কে ওই ছড়া প্রচার খুব কঠিন ছিল না,
বিশেষতঃ কামতাপুরে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে ইসলামের প্রভাব বিস্তারের সময়ে।
নিচুতলার ধর্মান্তরিত হিন্দু মুসলিম হলেও হিন্দু দেবদেবীর উল্লেখ থাকায়
ধর্মান্তরিত রাখাল কিশোর কিংবা ‘হালুয়া’ যাতে ভাওয়াইয়া গান না গায় তার
জন্যেই এই নিম্নরুচির ছড়ার প্রচার হয়েছিল বলে মনে করার যথেষ্ট আছে।
ভাওয়াইয়া গানের জন্মমুহূর্ত সম্পর্কে ঐতিহাসিক প্রমাণ দাখিল করা আমার
উদ্দেশ্য নয় এবং আমার তা অধিকার আছে বলেও মনে করছি না। আমি শুধু ভাবতে
চাইছি এই গানের প্রাচীনত্ব যদি কয়েক’শো বছরের হয় তাহলে তা গোটা বাংলায়
ছড়িয়ে পড়ে নি কেন? প্রাচীন গল্পগাথা সাহিত্য ইতিহাসে কেন ভাওয়াইয়ার মতো
প্রাণস্পর্শী গানের উল্লেখ নেই? সমাজের উঁচুতলার মানুষদের, বিশেষ করে
রাজ-রাজাদের দীর্ঘকাল ধরে অবজ্ঞার পাহাড়ের আড়ালে রেখেছে এই গানকে।
রাজন্যকৃপা বঞ্চিত ও উচ্চসমাজের অবহেলা-লাঞ্ছিত এই গান রাতারাতি জনপ্রিয়
হয়ে ওঠা যে সম্ভব ছিল না তা খুবই সহজবোধ্য ব্যাপার। উত্তরবাংলার (অখণ্ড)
বিশাল এলাকা জুড়ে এই গান যে দীর্ঘকালের স্বরচিত স্বশিক্ষিত একটা
ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসে আজও বেঁচে আছে তা বুঝতে পারি। যত দিন
গেছে ততই রাজবংশী সমাজ ধীরে ধীরে এই গান সর্বত্র নিজের প্রতিষ্ঠাকে দৃঢ় করে
তুলতে পেরেছে তার প্রাণবন্ত ভাব ও সুরমূর্ছনার গুণে।
বাংলা লোকসংস্কৃতির সুপ্রাচীন এক অন্যতম লোকগীতি হিসেবে ভাওয়াইয়া যে আজও
টিকে আছে তার নিজস্ব মাধুর্য ও প্রাণস্পর্শী আবেদন নিয়ে তার জন্য দায়ী
কিন্তু উচ্চসংষ্কৃতি কিংবা আদিম সংষ্কৃতির প্রবহমান সহায়তা নয়। কারণ
লোকসংষ্কৃতি বিষয় হিসেবে আধুনিক সমাজের উচ্চসাংস্কৃতিক ও আদিম সমাজের
সাংস্কৃতিক চরিত্র থেকে যথেষ্ট ভিন্ন। সামাজিক ক্রমানুবর্তনের পথ ধরে
মানবসভ্যতা ও সংষ্কৃতি বিকাশের একদিকে আদিম সমাজ ও তার কৃতি, অন্যদিকে
ক্রমোন্নত আধুনিক উচ্চ সমাজ, ঠিক এর মধ্যবর্তী স্তরের লোকসমাজের জীবনযাপন
পদ্ধতিজাত সংস্কৃতিই লোকসংষ্কৃতি। যা বহুকাল ধরে উচ্চসংষ্কৃতির বৃত্তের
বাইরে প্রাণের অকপট আবেগ উপলব্ধিতে বেঁচে থাকে। যেমন বেঁচে আছে ভাটিয়ালি,
ধামালী, মাঠ-কবি, চরের গান, বাউল গান--ইত্যাদি। ভাওয়াইয়াও ঠিক তেমনই এক গান
যা লোকসংস্কৃতি বা লোকগানের এক অন্যতম উজ্জ্বল সম্পদ হিসেবে টিকে আছে তার
নিজস্ব ভাব মাধুর্যের গুণে।
উত্তরবঙ্গে কিন্তু লোকসঙ্গীতের অভাব ছিল না একসময়ে। সারি গান, জাগ গান,
ভাটিয়ালি, হুদুমদেও’র গান ছাড়াও চোর-চুন্নি, বিষহরা সহ নানাবিধ
লোকগান-নাটকে সমৃদ্ধ ছিল উত্তরের জনপদ। এর মধ্যে কিন্তু ভাওয়াইয়া গানই ছিল
জনপ্রিয়তম সর্বাধিক প্রচারিত লোক গান। মূলতঃ দুটি, অর্থাৎ দরিয়া ও চটকা
আঙ্গিকে এবং সাধারণতঃ কার্ফা তালে ভাওয়াইয়া গাওয়া হয়। বিলম্বিত লয়ে দীর্ঘ
ছন্দে যে গান গাওয়া হয় তাকে দারিয়া এবং চটুল ও অপেক্ষাকৃত দ্রুত লয়ে গাওয়া
হয় চটকা। চিতান, ক্ষীরোল, দরিয়া ও দীঘলনাসা, গড়ান ও মইধালী--প্রধানতঃ এই
পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ভাওয়াইয়া গানকে। প্রেমবিষয়ক এই গানে রাধাকৃষ্ণ (কালা বা কালাচাঁদ) খুব বেশি গুরুত্ব পান
নি নায়ক-নায়িকা হিসেবে। প্রেমবিষয়ক ভাওয়াইয়া গানের নায়ক-নায়িকা হিসেবে আমরা
পাই সাধারণতঃ মৈষাল, গাড়িয়াল, মাহুত, বৈদ এবং নারী-কন্যাদের। এরা
একান্তভাবেই সমাজ ও ঘরসংসারের রক্তমাংসের চির চেনা চরিত্র। আমরা জানি ‘কানু
বিনা গীত নাই’ প্রবাদের জন্ম লৌকিক প্রেমের গানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমরসের
প্রাবল্য থেকেই। বাংলার অন্যান্য লোকগীতে রাধা-কৃষ্ণ প্রেম নিরপেক্ষ
সাধারণতঃ দেখা যায় না। ভাওয়াইয়া গানেই একমাত্র ব্যতিক্রম যেখানে পৌরাণিক
কোনো চরিত্র প্রাধান্য পায় নি।
হরিশচন্দ্র পাল সম্পাদিত ‘উত্তরবাংলার পল্লীগীতি’র ভাওয়াইয়া খণ্ডের ভূমিকা
লিখতে গিয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য স্পষ্টই বলেছেন,
‘কিন্তু উক্ত পৌরাণিক চরিত্রগুলি অবলম্বন করিয়া কোনও ভাওয়াইয়া গান রচিত হয় নাই। যদিও ভাওয়াইয়া গান প্রেমের গান এবং বাংলার প্রেমের গানের নায়ক-নায়িকামাত্রই রাধাকৃষ্ণ। তথাপি একমাত্র ভাওয়াইয়া গানই তাহার ব্যতিক্রম।’
এখানে অবশ্য সামান্য হলেও
একটু বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। কারণ, খুব বেশি না হলেও ভাওয়াইয়া গানে কালা,
কানাই, যমুনা (তোর্ষা, তিস্তা, কালজানি, মানসাই এসেছে ব্যাপকভাবে),
কদম্ববৃক্ষ, মোহনবাঁশি, এমন কী পরকীয়া প্রেমও এসেছে। এগুলো কিন্তু বহুল
কিংবা ব্যাপক নয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ভাওয়াইয়ার স্বাভাবিক ধারায় এগুলিকে
কোনো কোনো শিল্পী বা রচয়িতার খেয়ালী প্রয়াস কিংবা বিক্ষিপ্ত অনুপ্রবেশও বলা
যেতে পারে।
বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এমন বেশ কিছু ভাওয়াইয়া গান আছে। শুধু
বৈষ্ণবপদাবলী কেন--শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ময়মনসিংহ গীতিকার প্রভাবও কোন কোন গানে
পরিলক্ষিত হলেও তা কিন্তু ভাওয়াইয়ার সহজাত চারিত্রিক ধারা বৈশিষ্ট্যকে
লুপ্ত করার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নি কখনো। কারণ এগুলো এই অঞ্চলের
নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতির বিষয় ছিল না। অনেক পরে মূলতঃ দক্ষিণবঙ্গের
সাহিত্য-সঙ্গীতের সঙ্গে যখন থেকে এই অঞ্চলের অগ্রবর্তী উচ্চসমাজের সংযোগ
ঘটল এবং উচ্চসমাজের উচ্চসংষ্কৃতি হিসেবে গ্রহণীয় হয়ে উঠলো তখন থেকে
ভাওয়াইয়া গানে এই সংস্কৃতির কিছু কিছু অনুপ্রবেশ অনিবার্য্য হয়ে উঠেছিল
প্রধানতঃ সাক্ষর শিল্পী বা গীতিকারদের প্রচষ্টার ফলে।
অতি সাধারণ শিক্ষাদীক্ষাহীন গ্রাম্য গায়ক বা গীতিকারদের পক্ষে উচ্চসংষ্কৃতির বিষয়বস্তু আত্মস্থ করা ও তা নিজেদের ভাষায় ভাবে ও সুরে মিশিয়ে দেওয়া খুব সহজ ছিল না এবং সহজ ছিল না বলেই ভাওয়াইয়া তার নিজস্বতার ব্যাপকতা না হারিয়ে আজও বহুলাংশে নির্ভেজাল ভাওয়াইয়াই থেকে গেছে। এটা ঠিকঠাকভাবে বুঝতে গেলে ভাওয়াইয়ার নিজস্ব ক্ষেত্রটিকে বোঝা অত্যন্ত জরুরি। নিজস্ব ক্ষেত্রটিকে না বুঝলে তার নান্দনিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। যে লোকসংস্কৃতির উজ্জ্বল সম্পদ এই গান সেই লোকক্ষেত্রটির ক্রিয়াকলাপ তার ঐতিহাসিক পটপ্রকৃতি এবং তার নিজস্ব সাংষ্কৃতিক প্রেক্ষাপটেই তার তার গূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। প্রখ্যাত ভাওয়াইয়া গবেষক ও গায়ক সুখবিলাস বর্মার মতে,
‘ভাওয়াইয়া চটকা বলতে বুঝি অসমের পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরবাংলার উত্তরাঞ্চলে রাজবংশী সংষ্কৃতির সঙ্গীত, রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সুখ-দুঃখ-আশা-আনন্দ-বিষাদের গান--জীবনের গান।’
তাঁর এই মন্তব্য থেকেই
স্পষ্ট হচ্ছে ভাওয়াইয়া রাজবংশী জনগোষ্ঠীরই লোকগান। স্বভাবতই এই বিস্তীর্ণ
অঞ্চলের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সমাজচিত্রটা বহু প্রচারিত অজস্র এই গানের ভেতর
থেকেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। কি নেই এই প্রাণস্পর্শী গানের মধ্যে? সমাজের
উৎসব অনুষ্ঠানের ছবি, পাখি, নদী, প্রকৃতি, লতা-বৃক্ষ, নদীর চর--সর্বোপরি
নর-নারীর প্রেম বিরহ ইত্যাদি সবই যা অনুভবের মধ্য দিয়ে গোটা প্রেক্ষাপটকেই
স্পষ্ট করে তুলতে পারে।
দশম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর সাহিত্য-সংষ্কৃতির ইতিহাসে ভাষা হিসেবে বাংলার
বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। সেকালে বিদ্যা বা সংষ্কৃতিচর্চার
কেন্দ্র ছিল মূলতঃ বৌদ্ধবিহার এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের গৃহ বা চতুস্পাঠী।
রাজা-জমিদারদের পৃষ্ঠপোষণায় কাব্য সাহিত্য চর্চা হত প্রধানতঃ সংষ্কৃত
ভাষায়, যা উচ্চ সংষ্কৃাতির নিত্য পরিবর্তনশীলতার বাইরের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর
মন্থর জীবনগতিতে প্রবহমান সংস্কৃতির ভাষার সঙ্গে কোনোভাবেই তুলনীয় ছিল না।
সেদিক থেকে দেখতে গেলে লোক সংষ্কৃতি সাধারণতঃ উচ্চসংস্কৃতির বিপরীত কোটির
সংস্কৃতি। তাই পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর সময়কালে কয়েকজন সুলতান যখন
নিজেদের সভায় বাঙালি কবি-শিল্পীকে কাব্য-কবিতা-গান রচনায় উৎসাহিত করছেন তখন
স্বভাবতঃই সেই সব কাব্য-কবিতা-গানের বিষয় ছিল ধর্মাশ্রয়ী কৃষ্ণের
বৃন্দাবনলীলা কিংবা ঐতিহাসিক গাথা ইত্যাদি। বাংলা সাহিত্যের প্রায় ঊষালগ্নে
গেয় কাব্য বা কবিতারই ছিল প্রাধান্য। এক কথায় বলতে গেলে গান।
ভাওয়াইয়ার অস্তিত্ব ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর সময়কাল বলে যদি ধরে নেওয়া
হয় তাহলে বলতেই হবে ‘পাতার বাড়ির গান’ (প্রান্তবাসী/প্রান্তিক) হিসেবে
দীর্ঘকাল উপেক্ষিত ভাওয়াইয়া গানই বাংলা (বাংলা বলে যারা মানেন না তাদের
প্রতি সম্মান রেখেই) গেয় (কবিতা) সাহিত্যের সেই মূল্যবান প্রথম নিদর্শন যা
বিশুদ্ধ নর-নারীর প্রেম নিয়ে উচ্চকিত ছিল এবং বলা বাহুল্য--নর-নারীর জাগতিক
প্রেম নিয়ে উচ্চকিত হওয়া তখন রীতিমতো নিন্দনীয় ছিল! ধর্মাশ্রয়ী সাহিত্য যখন মুষ্টিমেয় উচ্চসংষ্কৃতির মানুষের চর্চার বিষয়
তখন একমাত্র ভাওয়াইয়াই অতি সাধারণ মানুষের প্রেম-বিরহ-হাসি-কান্নাকে
অবলম্বন করে বিস্তৃত অঞ্চলকে মাতিয়ে রেখেছিল। কিন্তু যেহেতু উচ্চসংষ্কৃতি ও
লোকসংস্কৃতির মধ্যে আভিজাত্যবোধের পার্থক্য ছিল (এখনও আছে) এবং
উচ্চসংস্কৃতির মধ্যে যে মার্জিত মানসিকতার ভাব বিদ্যমান থাকতো তা
প্রান্তবাসী লোকজীবনের অকপট সরল প্রকাশভঙ্গিতে অনুপস্থিত ছিল, তাই
ভাওয়াইয়াকে এই সেদিনও উচ্চসমাজ-স্বীকৃত সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য করা হত না।
ভাওয়াইয়াকে অন্যতম উজ্জ্বল গেয় সাহিত্য হিসেবে পাদপ্রদীপের সামনে নিয়ে আসেন
প্যারীমোহন দাস, আব্বাসউদ্দিন, নায়েব আলি টিপু, সুরেন বসুনীয়া, শৈলেন রায়,
টগর অধিকারী, ধনেশ্বর রায়, সুখবিলাস বর্মা প্রমুখ অনেকেই। উচ্চশিক্ষিত একজন
আইএএস হয়েও সুখবিলাস বর্মা যখন দোতরার টুংটাং শব্দের মায়াময়তায় নিজেকে
হারিয়ে ফেলেন এক অদ্ভুত আবেগে তখন অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে হয় তাঁর ভাববিহ্বল
সেই উজ্জ্বল মুখের দিকে। তখন এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, রাজবংশী সমাজের শিক্ষিত
মানুষের আবেগের ছোঁয়া যতদিন পাবে ততদিন ভাওয়াইয়া গানও বেঁচে থাকবে তার
স্বমহিমায়!
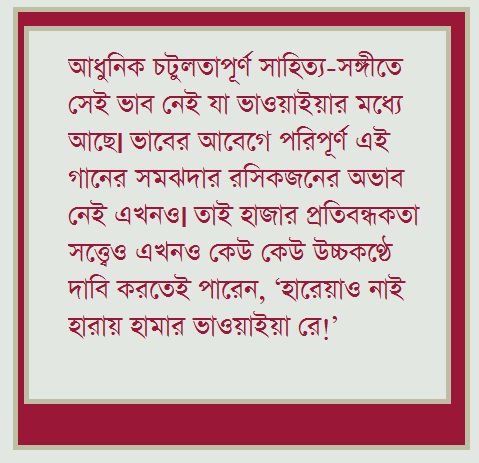 নিজে শিল্পী নন, কিন্তু উত্তরবঙ্গের সংষ্কৃতির সঙ্গে যাঁর প্রাণের যোগ
বর্তমান--সেই দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী হিসেবে যোগ
দিয়েই ভাওয়াইয়াকে গোটা রাজ্যের মানুষের কাছে প্যেঁছে দেওয়ার যে ফলপ্রসূ
চেষ্টা করেছিলেন তার ফলেই আজ প্রতিবছর ভাওয়াইয়া রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত
হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে বহু ছেলে-মেয়ে। প্রতিটি রাজ্যসম্মেলনে গভীর
রাত পর্যন্ত মানুষের বিপুল সমাগমই প্রমাণ করে এই ভাওয়াইয়ার রাজ্য সম্মেলনের
কতটা প্রয়োজন ছিল!
নিজে শিল্পী নন, কিন্তু উত্তরবঙ্গের সংষ্কৃতির সঙ্গে যাঁর প্রাণের যোগ
বর্তমান--সেই দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী হিসেবে যোগ
দিয়েই ভাওয়াইয়াকে গোটা রাজ্যের মানুষের কাছে প্যেঁছে দেওয়ার যে ফলপ্রসূ
চেষ্টা করেছিলেন তার ফলেই আজ প্রতিবছর ভাওয়াইয়া রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত
হচ্ছে। প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে বহু ছেলে-মেয়ে। প্রতিটি রাজ্যসম্মেলনে গভীর
রাত পর্যন্ত মানুষের বিপুল সমাগমই প্রমাণ করে এই ভাওয়াইয়ার রাজ্য সম্মেলনের
কতটা প্রয়োজন ছিল!
শিক্ষা, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার প্রসার রাজবংশী সমাজে যত বিস্তৃত হচ্ছে
রাজবংশী সমাজের নিজস্ব লোকসংষ্কৃতির প্রতি উদাসীনতাও কিন্তু পাল্লা দিয়ে
বাড়ছে। বাড়ছে রবীন্দ্রসঙ্গীত, আধুনিক বাংলা, হিন্দি গানের শিল্পী হওয়ার ঝোঁক।
বাড়ছে কলকাতামুখী ব্যাণ্ড-শিল্পী হওয়ার জন্য অস্থিরতা। রবীন্দ্রসঙ্গীত
শিক্ষা কিংবা অন্যান্য যে কোন সঙ্গীত শিক্ষা মোটেও নিন্দনীয় নয়--বরং
প্রতিভা বিকাশেরই ভিন্ন ভিন্ন পথ। উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের
সিংহভাগ মঞ্চ অধিকার করে রাখছে ব্যাণ্ড-হিন্দি এবং আধুনিক চটুল অরুচিকর
উগি-বুগি সংষ্কৃতি। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ সবসময়েই আপেক্ষিক বিষয়। কিন্তু
নিজস্ব সংষ্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধতার প্রশ্নকে উড়িয়ে দিয়ে নিজেদের
সংষ্কুতিবান করে তোলা যায় কিনা সেটাও ভাবা একইসঙ্গে জরুরি। ভাওয়াইয়া গানের
অনুষ্ঠান নিয়মিত দূরদর্শনে, বাংলার সরকারি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমঞ্চে
প্রচারিত হওয়া দরকার।
একথা ঠিকই যে, একদা ভাওয়াইয়া গানে রাজবংশী সমাজের যে চিত্র ছবির মতো ফুটে উঠতো এখন তার অনেক কিছুই নেই। এ প্রসঙ্গে সুখবিলাস বর্মা বলেছেন,
‘এমন কী পুরানো ভাওয়াইয়া চটকা গানে রাজবংশী জীবনের খুঁটিনাটি যেভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যেত আজ আর তেমনটি পাওয়া যায় না। দরিয়া ভাওয়াইয়ার সেই দরদ, সেই গভীরতা, বিষাদময়তা আজ অনুভূত হয় না। সেই কারণেই ধনেশ্বর মাস্টারমশাই গেয়েছেন ভাওয়াইয়া গান--আজি হারেয়া গেইছে রে। পুরানো ভাওয়াইয়ার রসদ কোড়া, কুড়ি, বগা, বালি হাঁস, কুরুয়া পাখিরা কোথায় গেল রে। কোথায় গেল ভরযুবতী নারী, চিটুল বিদুয়ার সীমাহীন দুঃখের জীবন অথবা সাঙানির ধিকি ধিকি মানরে জ্বালা? মাস্টার মশাইয়ের গানটির স্টাইল ও কথাগুলোর অনুসরণে উত্তরবঙ্গের সাংস্কৃতিক জীবন থেকে কত মূল্যবান বস্তু ধীরে ধীরে বিলীন হতে চলেছে তা এক এক করে তালিকাভুক্ত করার চেষ্টা করা যেতে পারে।’
বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে এ সত্য অস্বীকারের উপায় নেই। উচ্চশিক্ষা এবং অত্যাধুনিকতার ছোঁয়ায় রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতি মনন ঐতিহ্য দ্রুত বদলে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তবু যাঁরা মনে করছেন তাঁদের নিজস্ব সংষ্কৃতির মূল্যবান সম্পদগুলিকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করা দরকার এবং বাঁচিয়ে রাখা দরকার, সংখ্যায় অল্প হলেও তাঁরা সে চেষ্টা করে যাচ্ছেন আনুষ্ঠানিকতা সর্বস্বতার মধ্যেও। আধুনিক চটুলতাপূর্ণ সাহিত্য-সঙ্গীতে সেই ভাব নেই যা ভাওয়াইয়ার মধ্যে আছে। ভাবের আবেগে পরিপূর্ণ এই গানের সমঝদার রসিকজনের অভাব নেই এখনও। তাই হাজার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এখনও কেউ কেউ উচ্চকণ্ঠে দাবি করতেই পারেন, ‘হারেয়াও নাই হারায় হামার ভাওয়াইয়া রে!’