.............
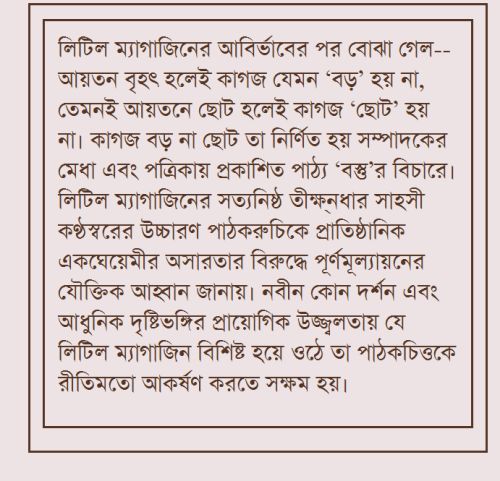 লিটিল
ম্যাগাজিনের ইতিহাস ঘাঁটতে ঘাঁটতে যেদিন দেখলাম টি এস এলিয়ট এবং জেমস্
জয়েস-এর বিশ্বখ্যাত দুটি উপন্যাস ‘ওয়েস্টল্যাণ্ড’
এবং ‘ইউলিসিস’
নামে দুটি লিটিল ম্যাগাজিনে প্রথম ছাপা হয় ও প্রকাশিত হয় তখন
বাস্তবিকই বিস্ময়ের আধিক্যে রীতিমতো উত্তেজনা বোধ করেছিলাম। লেখালেখি এবং
পত্রপত্রিকার ইতিহাসে লিটিল ম্যাগাজিনের আবির্ভাব মাত্রই ১৮০ বছর আগে।
মোটামুটি বিংশ শতাব্দীর শুরুতে লিটিল ম্যাগাজিনের প্রসার ও প্রচার শুরু
হলেও এর আদি চেহারাটা দেখা গিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৮৪০-১৮৪৪)
সময়ে।
লিটিল
ম্যাগাজিনের ইতিহাস ঘাঁটতে ঘাঁটতে যেদিন দেখলাম টি এস এলিয়ট এবং জেমস্
জয়েস-এর বিশ্বখ্যাত দুটি উপন্যাস ‘ওয়েস্টল্যাণ্ড’
এবং ‘ইউলিসিস’
নামে দুটি লিটিল ম্যাগাজিনে প্রথম ছাপা হয় ও প্রকাশিত হয় তখন
বাস্তবিকই বিস্ময়ের আধিক্যে রীতিমতো উত্তেজনা বোধ করেছিলাম। লেখালেখি এবং
পত্রপত্রিকার ইতিহাসে লিটিল ম্যাগাজিনের আবির্ভাব মাত্রই ১৮০ বছর আগে।
মোটামুটি বিংশ শতাব্দীর শুরুতে লিটিল ম্যাগাজিনের প্রসার ও প্রচার শুরু
হলেও এর আদি চেহারাটা দেখা গিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৮৪০-১৮৪৪)
সময়ে।
বস্টন শহরে র্যালফ্ ওয়ালডো এমারসন ও মার্গারেট ফুলার-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘দ্য ডায়াল’ নামে একটি ছোট পত্রিকা--যাকে সাহিত্য জগতের বিদগ্ধরা লিটিল ম্যাগাজিনের আদি রূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই ‘দ্য ডায়াল’ পত্রিকাতেই এলিয়টের বিখ্যাত ‘ওয়েস্টল্যাণ্ ‘ উপন্যাস প্রথম ছাপা হয়! পত্রিকাটিতে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং কবিতাও ছাপা হত। সাহিত্যের এই পত্রিকার ললাটে ‘লিটিল ম্যাগাজিন’ শব্দটি কেন সেঁটে গেল তা জানতে হলে বেশ খানিকটা পিছনে তাকাতে হয়।
আরও প্রায় ১০০ বছর আগে ১৭৩১ সালে এডওয়ার্ড কেভ-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বোর্ড বাঁধানো ‘জেন্টলম্যানস্ ম্যাগাজিন’ নামে একটি পত্রিকা। ইংরেজি ম্যাগাজিন শব্দের অর্থ ‘বারুদশালা’। বারুদশালার মতোই শব্দ-অক্ষরের মালমশলা ঠাসা পত্রিকাকে ‘ম্যাগাজিন’ শব্দরূপ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করার ব্যাপারটা কিন্তু বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রথমে বাঁধানো পত্রিকাকে ‘ম্যাগাজিন’ বললেও পরবর্তীতে যে কোনো পত্রিকাকেই ম্যাগাজিন বলা শুরু হয়েছিল। কিন্তু ‘লিটিল’ এবং ‘ম্যাগাজিন’ এই দুই শব্দকে একসঙ্গে জুড়ে ‘লিটিল ম্যাগাজিন’ নামে উচ্চারণ শুরু হয় ইউরোপে আঠারো শতকের শেষে অথবা ঊনিশ শতকের শুরু থেকেই বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।
বৃহৎ পুঁজির পণ্যসর্বস্ব সাহিত্যের বিপরীতে নতুন ভাবনা চিন্তা সমৃদ্ধ আধুনিক সাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচেষ্টা যে সব পত্রিকার বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল প্রধানতঃ সেইসব পত্র-পত্রিকাকেই ‘লিটিল ম্যাগাজিন’ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। লিটিল ম্যাগাজিন ঠিক কেমন হতে পারে তার সফল দৃষ্টান্ত হিসেবে এখনও মার্গারেট এণ্ডারসন সম্পাদিত ‘দ্য লিটিল রিভিয়্যু’ (শিকাগো, সানফ্রান্সিস্কো, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস--১৯১৪-১৯২৯) পত্রিকার কথাই বলা হয়ে থাকে। এই পত্রিকাতেই জেমস্ জয়েস্-েএর ‘ইউলিসিস’ উপন্যাসের প্রথম ১১ পর্ব ছাপা হয়েছিল!
লিটিল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে--পেয়েট্রি (১৯১২), দ্য ইগোয়িস্ট (১৯১৪-১৯২৯/লণ্ডন) নিউ ম্যাসেস (১৯২৬-১৯৪৮), দ্য অ্যানভিল (১৯৩৩-১৯৩৯), ব্লাস্ট (১৯৩৩-১৯৩৪), নিউ ভার্স (১৯৩৩-১৯৩৯), ক্রিটেরিয়োঁ (১৯২২-১৯৩৯)--ইত্যাদি পত্রিকাগুলি নিজস্ব উজ্জ্বলতায় স্মরণীয় হয়ে আছে। এইসব পত্রিকাতেই বিশ্বসাহিত্যের নক্ষত্রদের অন্যতম--এজরা পাউণ্ড, টি এস এলিয়ট, জেমস্ জয়েস্, হেমিংওয়ে সহ অনেকেই সৃজনশীল সাহিত্যের বিচিক্রমুখী চর্চা করে গেছেন। লিটিল ম্যাগাজিনের এই তালিকায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গদর্শন’কে (১৮৭২) যুক্ত করলেও বাংলায় লিটিল ম্যাগাজিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ কছিল প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত ‘সবুজপত্র’ (১৯১৪) পত্রিকাটি।
বিশেষজ্ঞরা লিটিল ম্যাগাজিনের যথার্থ চরিত্র নির্ণয় করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছেন এগুলি প্রধানতঃ প্রতিবাদী ও প্রতিষ্ঠানবিরোধী। তাই প্রথাবিরোধী নতুন দর্শন এবং দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৃষ্টিশীল সাহিত্য চর্চার হাতিয়ার হয়ে ওঠে এই লিটিল ম্যাগাজিন। সাহিত্যের আধুনিক গতিপ্রকৃতি, আনকোড়া উপস্থাপন (মূলতঃ তরুণ সাহিত্যিকদের), সাহিত্যের বিচিত্রমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রতিফলিত হতে থাকে লিটিল ম্যাগাজিনে।
বাংলা লিটিল ম্যাগাজিনের আলোচনায় অনিবার্য ভাবেই উঠে আসে বুদ্ধদেব বসুর নাম। পঞ্চাশের দশকে বাংলাভাষায় ইংরেজির প্রভাবে লিটিল ম্যাগাজিন শব্দবন্ধটি প্রথম ব্যবহার করেন বুদ্ধদেব বসু-ই। যদিও তখন-ই এই অভিধা ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হয় নি। তবে ১৯৫৩ সালের মে মাসে ‘দেশ’ পত্রিকার একটি সংখ্যায় বুদ্ধদেব বসু ‘সাহিত্যপত্র’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লিটিল ম্যাগাজিনের যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা অবশ্যই সংগ্রহ করে বার বার পড়া উচিত আজকের লিটিল ম্যাগাজিন সম্পাদকদের। কিন্তু অনেকেই খবর রাখেন না এই মূল্যবান প্রবন্ধটির। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন--‘ভালো লেখা বেশি জন্মায় না, সত্যিকার নতুন লেখা আরো বিরল; আর শুধু দুর্লভের সন্ধানী হলে পৃষ্ঠা ও পাঠক সংখ্যা কমে আসে। অর্থাৎ আমরা যাকে বলি সাহিত্যপত্র, খাঁটি সাহিত্যের পত্রিকা, লিটিল ম্যাগাজিন তারই আরো ছিপছিপে ব্যঞ্জনাবহ নতুন নাম।’
লিটিল ম্যাগাজিনের আবির্ভাবের পর বোঝা গেল--আয়তন বৃহৎ হলেই কাগজ যেমন ‘বড়’ হয় না, তেমনই আয়তনে ছোট হলেই কাগজ ‘ছোট’ হয় না। কাগজ বড় না ছোট তা নির্ণিত হয় সম্পাদকের মেধা এবং পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ্য ‘বস্তু’র বিচারে। লিটিল ম্যাগাজিনের সত্যনিষ্ঠ তীক্ষ্নধার সাহসী কণ্ঠস্বরের উচ্চারণ পাঠকরুচিকে প্রাতিষ্ঠানিক একঘেয়েমীর অসারতার বিরুদ্ধে পূর্ণমূল্যায়নের যৌক্তিক আহ্বান জানায়। নবীন কোন দর্শন এবং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রায়োগিক উজ্জ্বলতায় যে লিটিল ম্যাগাজিন বিশিষ্ট হয়ে ওঠে তা পাঠকচিত্তকে রীতিমতো আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। বাংলা লিটিল ম্যাগাজিনের ইতিহাস ঘাঁটলে এই সত্যের অজস্র প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যের বহু খ্যাতিমান লেখক তৈরির কৃতীত্ব রয়েছে লিটিল ম্যাগাজিনের।
প্রধানতঃ লিটিল ম্যাগাজিনের লেখক হিসেবেই যাঁর নাম পরিচিত তিনি উত্তরবঙ্গের কোচবিহারের প্রয়াত সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার। অত্যন্ত শক্তিশালী ও ব্যতিক্রমী এই লেখক নিজেকে লিটিল ম্যাগাজিনের লেখক হিসেবে পরিচয় দিতেই বেশি গর্ব বোধ করতেন।
জন ক্লার্ক মার্শম্যানের ‘দিকদর্শন’ (১৮১৮) দিয়েই বাংলায় পত্রপত্রিকার যাত্রা শুরু হয়। তারপর একে একে--বঙ্গদর্শন (১৮৭২), ভারতী (১৮৭৭), হিতৈষী (১৮৭৮), সাহিত্য (১৮৯০), প্রবাসী (১৯০১), ভারতবর্ষ (১৯১০) সহ অনেক পত্রপত্রিকা পরবর্তীতে লিটিল ম্যাগাজিন প্রকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। প্রথাবিরোী মননশীল রচনা নিয়ে লিটিল ম্যাগাজিন আন্দোলন গড়ে ওঠার পক্ষে এইসব পত্রিকার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
প্রথাবিরোধী মননশীল রচনা সমৃদ্ধ যথার্থ লিটিল ম্যাগাজিনের চেহারা নিয়ে ‘সবুজপত্র’-এর আত্মপ্রকাশের পর একে একে--কল্লোল (১৯২৩), শনিবারের চিঠি (১৯২৪), সওগাত (১৯২৬), শিখা (১৯২৭), কালি কলম (১৯২৭), প্রগতি (১৯২৭), পরিচয় (১৯৩১), পূর্বাশা (১৯৩২), কবিতা (১৯৩৫), চতুরঙ্গ (১৯৩৮) ইত্যাদি পত্রিকার আত্মপ্রকাশ বাংলা সাহিত্যকে কীভাবে গতিশীল করেছিল তা ঐ পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত রচনা সম্ভার দেখলেই বোঝা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস ‘পদ্মানদীর মাঝি’ পূর্বাশা পত্রিকায় মাত্র ১০০ টাকার (সংখ্যাপ্রতি) সম্মান দক্ষিণার বিনিময়ে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। ‘গণবাণী’ পত্রিকায় কাজী নজরুলকে প্রাথমিক গুরুত্ব না দিলে কি হত বলা কঠিন। পূর্বাশা পত্রিকা লেখক হিসেবে অমিয়ভূষণকেও প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গেই। এরকম বহু পত্রপত্রিকা (ক্ষণজীবি) বহু লেখককে তুলে এনে প্রতিষ্ঠার পথে যাত্রা করিয়ে দিয়েছে। প্রাক্ স্বাধীনতার সাহিত্য-সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র কলকাতা হওয়ায় প্রায় সব উল্লেখযোগ্য পত্রিকাই আত্মপ্রকাশ করেছে কলকাতা থেকেই। শুধুমাত্র বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত ‘প্রগতি’ এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ‘পূর্বাশা’ কুমিল্লা থেকে আত্মপ্রকাশ করে।
১৯৪৭-এ দেশ বিভাজনের পর ৫০-এর দশকে বাংলাদেশে লিটিল ম্যাগাজিনের তেমন উল্লেখযোগ্য খবর নেই। কয়েকটি পত্রিকা অবশ্য প্রকাশিত হয়েছিল যার মধ্যে উল্লেখ করতে হবে--কবিকণ্ঠ (ফজল শাহাবুদ্দিন), সমকাল (সিকান্দার আবু জাফর), অগত্যা (ফজলে লোহানী), সীমান্ত (মাহবুবুল আলম চৌধুরী), উত্তরণ (এনামূল হক) ইত্যাদি। এর মধ্যে সমকাল প্রতিবাদী-মননশীল পত্রিকা হিসেবে খ্যাতি কুড়িয়েছিল। ষাটের দশকেও বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা প্রকাশিত হলেও বাংলাদেশের লিটিল ম্যাগাজিনের জোয়ার আসে ৭১-এর দ্বিতীয় স্বাধীনতার পর। অসংখ্য উঁচু মানের পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে বাংলাদেশে। সেগুলি বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রকে রীতিমতো সমৃদ্ধ করেছে।
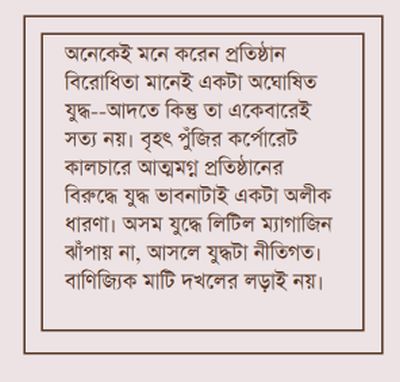 আগেই
বলেছি,
লিটিল ম্যাগজিনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠান
বিরোধিতা ও অ-প্রাতিষ্ঠানিকতা। এই অ-প্রাতিষ্ঠানিকতার চরিত্র অটুট রাখতে
গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিষ্ঠানবিরোধী একটা প্রবণতা চলে আসে--যা কিন্তু
মুখ্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিছু নয়। প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি কখনোই
মানুষের চিন্তা চেতনার জগতকে পুরোপুরি আলোকিত করার দায় বা ‘ঠিকা’
নেয় না। তাদের
প্রধান উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যমুখিনতাকে দৃঢ়তর করা। এর জন্যেই দেখা
যায় অখ্যাত লিটিল ম্যাগাজিন থেকে উঠে আসে সম্ভাবনাময় লেখকদের তুলে এনে
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে গতিশীল করার কাজে তাদের ব্যবহার করতে।
আগেই
বলেছি,
লিটিল ম্যাগজিনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠান
বিরোধিতা ও অ-প্রাতিষ্ঠানিকতা। এই অ-প্রাতিষ্ঠানিকতার চরিত্র অটুট রাখতে
গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিষ্ঠানবিরোধী একটা প্রবণতা চলে আসে--যা কিন্তু
মুখ্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিছু নয়। প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি কখনোই
মানুষের চিন্তা চেতনার জগতকে পুরোপুরি আলোকিত করার দায় বা ‘ঠিকা’
নেয় না। তাদের
প্রধান উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যমুখিনতাকে দৃঢ়তর করা। এর জন্যেই দেখা
যায় অখ্যাত লিটিল ম্যাগাজিন থেকে উঠে আসে সম্ভাবনাময় লেখকদের তুলে এনে
প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে গতিশীল করার কাজে তাদের ব্যবহার করতে।
এঁদের সৃষ্টিশীলতা এবং স্বাধীনতা সাংঘাতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থেই। স্বার্থের পক্ষে যেসব লেখকদের ‘সৃষ্টিশীলতা’ বিশেষ কাজে লাগে না তাঁদের ঠাঁই-নড়া হতে বেশি সময় লাগে ন। লিটিল ম্যাগাজিন ঠিক এই জায়গাটিতেই নিজের চরিত্র বজায় রেখে চলেছে তাদের অ-বাণিজ্যমুখী সাহিত্যচর্চার নিষ্ঠাকে পুঁজি করে। অনেকেই মনে করেন প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা মানেই একটা অঘোষিত যুদ্ধ--আদতে কিন্তু তা একেবারেই সত্য নয়। বৃহৎ পুঁজির কর্পোরেট কালচারে আত্মমগ্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ভাবনাটাই একটা অলীক ধারণা। অসম যুদ্ধে লিটিল ম্যাগাজিন ঝাঁপায় না, আসলে যুদ্ধটা নীতিগত। বাণিজ্যিক মাটি দখলের লড়াই নয়।
সামান্য পুঁজি সম্বল করে এখনও লিটিল ম্যাগাজিনই প্রত্যন্ত থেকে তুলে আনছে কবি গল্পকার প্রাবন্ধিকদের। যাদের মধ্যে ‘মশলা’ আছে প্রতিষ্ঠান তাদের তুলে নিতে দেরি করে না। প্রকৃতপক্ষে লিটিল ম্যাগাজিন কিন্তু প্রতিষ্ঠানেরই প্রাথমিক দায়িত্বটুকু বহন করে চলেছে গাঁটের কড়ি খরচ করে! এ প্রসঙ্গে আলোচক বন্ধু তপোধীর ভট্টাচার্যের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য--‘এই জন্য লিটিল ম্যাগাজিন নিছক ইতিহাসের উপকরণমাত্র নয়, আসলে তা হলো ইতিহাসের নির্মাতা। বার বার আমাদের প্রচলিত অভ্যাসে হস্তক্ষেপ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে বেপরোয়া অন্তর্ঘাত করে, সাহিত্যের পথ থেকে পলি সরিয়ে দিয়ে তা তীব্র ও দ্যুতিময় নবীন জলধারাকে গতিময় করে তোলে। একই কারণে ছোট পত্রিকাকে আত্মবিনির্মাণপন্থী না হলে চলে না। কেননা কখনো কখনো, নিজেরই সযত্নরচিত পদ্ধতি প্রকরণ ও অন্তর্বস্তু প্রাতিষ্ঠানিক স্বভাব অর্জন করে নেয়, তখন নির্মোহভাবে নিজেকে আঘাত করে জটাজাল থেকে প্রাণের গল্পকে মুক্ত করতে হয়।
সাহিত্যের মূল্যবোধ আসলে সমাজের উঁচুতলার স্বার্থপোযোগী ও স্বার্থানুমোদিত মূল্যবোধ। তাই ঐ মূল্যবোধকে তীক্ষ্ন জিজ্ঞাসার তীরে বিদ্ধ না করে, ঐ মূল্যবোধের আশ্রয় হিসেবে গড়ে ওঠা ভাষা-প্রকরণ-সন্দর্ভকে আক্রমণ না করে কোনো নতুন সম্ভাবনার জন্ম হতে পারে না।’
অতএব পুরনো মূল্যবোধকে
আক্রমণ করে নতুন দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাহিত্যকে প্রাণবন্ধ ও গতিশীল
করতে গিয়ে যে লড়াই এবং আন্দোলন গড়ে তুলতে হয় তাতে বহু পত্রিকারই আয়ু ক্ষীণ
থেকে ক্ষীণতর হয়ে ওঠে।
এতে যে হিমালয়ানপ্রমাণ অর্থনৈতিক সহায়তা শূন্য পুঁজির সঙ্কট সব সময়েই থেকে
যায়!